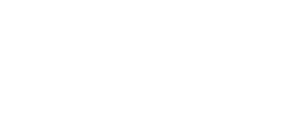লেখা। পিয়ের প্রকাশ, এশিয়ার প্রোগ্রাম ডিরেক্টর।
কোটা পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী শিক্ষার্থীদের ওপর দমন-পীড়ন শুরু করে নিরাপত্তা রক্ষাকারীরা। এতে ১৬ই জুলাই থেকে সারা
বাংলাদেশে কমপক্ষে ২০০ জন নিহত এবং হাজার হাজার আহত হয়েছেন। জুলাইয়ের শুরুতে বিক্ষোভ শুরু হওয়ার পর থেকে, কয়েক হাজার শিক্ষার্থী এবং সহানুভূতিশীলরা আদালতের একটি সিদ্ধান্তে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে রাস্তায় নামেন। কারণ, নিম্ন আদালত তার রায়ে সরকারি চাকরিতে ৩০ শতাংশ কোটা পুনর্বহাল রাখে ১৯৭১ সালের মুক্তিযোদ্ধাদের বংশধরদের জন্য। এই কোটা সংস্কারের জন্য বিক্ষোভে সরকারের সহিংস প্রতিক্রিয়া আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছে। এটিকে অন্তত এক দশকের মধ্যে বাংলাদেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত করেছে এবং সম্ভবত ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকে সবচেয়ে গুরুতর চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। এই বিক্ষোভ এমন এক সময়ে আসে যখন বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত অব্যবস্থাপনা এবং দুর্নীতির কারণে টালমাটাল, যার ফলে বেসরকারি খাতে তরুণদের চাকরির সুযোগ কমছে। সেইসঙ্গে সরকারের কর্তৃত্ববাদের জেরে বাড়ছে ক্রমবর্ধমান হতাশা।
সংকট মূলত সরকারের তৈরি। এর প্রাথমিক দমন-পীড়নের নৃশংসতা এবং প্রতিবাদী ছাত্রদের সম্পর্কে শীর্ষ কর্মকর্তাদের অবমাননাকর মন্তব্য শুধুমাত্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে, বিক্ষোভের আকার বাড়িয়েছে এবং ছাত্রনেতাদের তাদের দাবিগুলো প্রসারিত করতে প্ররোচিত করেছে। ১৮ই জুলাই ছাত্ররা দেশব্যাপী ‘ব্লকেড’র ডাক দিলে উত্তেজনা চরমে ওঠে এবং পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলা চালায়, কয়েক ডজন তরুণকে হত্যা করে।
বিজ্ঞাপন
রক্তপাতের সেই ছবি ছড়িয়ে পড়েছিল সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফরমগুলোতে। বিক্ষোভকারীদের সংগঠিত করা থেকে বিরত রাখতে- বিশেষ করে ফেসবুক গ্রুপের মাধ্যমে- সরকার সেই রাতে অবিলম্বে দেশব্যাপী ইন্টারনেট বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৭ কোটি মানুষকে অনলাইন সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। পরের দিন, বিক্ষোভ বড় আকার ধারণ করে, বিশেষ করে রাজধানী ঢাকায়, যেখানে অনেক বিক্ষুব্ধ নাগরিক ছাত্র মিছিলে যোগ দেয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি কঠোর কারফিউ ঘোষণা করেন, দিনে কয়েক ঘণ্টা বাদে নাগরিকদের ঘরের মধ্যে আটকে থাকতে বাধ্য করেন। তিনি দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ দিয়ে সেনাবাহিনীকে রাস্তায় নামানোয় ১৯ থেকে ২১শে জুলাই পর্যন্ত ১০০ জনেরও বেশি লোককে হত্যা করা হয়, এবং বেশ কয়েকজন প্রতিবাদী নেতাকে অপহরণ করা হয়।
কর্তৃপক্ষও বিক্ষোভকারীদের শান্ত করতে উঠেপড়ে লাগে। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গিয়ে ২১শে জুলাই সরকারি চাকরিতে কোটা কমানোর আদেশ দেয়। সরকার একটি স্বাধীন তদন্তের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং একজন মন্ত্রী দাবি করেছেন যে, সহিংসতার জন্য দায়ী প্রত্যেককে জবাবদিহি করা হবে। তবুও আইনি প্রক্রিয়া বা ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে সরকারের দমনমূলক প্রতিক্রিয়ার কঠোরতা, বিক্ষোভকে নীরব করে দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। ২২শে জুলাই ছাত্র নেতারা নতুন দাবি জানান। তবে তাদের বিক্ষোভে ৪৮ ঘণ্টা বিরতি ঘোষণা করা হয়, যা তারা আরও ৪৮ ঘণ্টা বাড়িয়েছেন। ঢাকার হাসপাতালে গুলিবিদ্ধ মৃতদেহের সংখ্যা কমছে এবং স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে। সরকার সীমিত ইন্টারনেট সুবিধা পুনরুদ্ধার করেছে, কারফিউ ধীরে ধীরে শিথিল করা হয়েছে এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম আংশিকভাবে আবার শুরু হয়েছে। রাজধানীতে ফিরে এসেছে সেই ‘ট্রাফিক জ্যাম’। তবে, অস্থিরতার ফল এখন টের পাওয়া যাচ্ছে। যদিও সরকার জোর দিয়ে বলেছে যে, মাত্র কয়েক ডজন মারা গেছেন। বিশ্বাসযোগ্য রিপোর্টে নিশ্চিত মৃত্যুর সংখ্যা ১৯০ থেকে ২০২ এর মধ্যে। প্রকৃত সংখ্যা অনেক বেশি হতে পারে; ইন্টারনেট বন্ধের ফলে সারা দেশে অশান্তির একটি সম্পূর্ণ চিত্র সংগ্রহ করা অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে।
সরকারের শীর্ষ কর্মকর্তারা বিরোধী দলগুলোকে, বিশেষ করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং জামায়াতে ইসলামীকে হিংসাত্মক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য দায়ী করেছে। নিরাপত্তা বাহিনী ৩,০০০ জনেরও বেশি লোককে গ্রেপ্তার করেছে বলে জানা গেছে- যার মধ্যে কিছু ছাত্রনেতা কিন্তু প্রধানত বিএনপি ও জামায়াতের কর্মকর্তারা রয়েছেন এবং ৬০,০০০ জনেরও বেশি লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে। যদিও সরকার তার দাবির সমর্থনে সামান্য প্রমাণ সরবরাহ করেছে যে বিএনপি ও জামায়াত বিক্ষোভ চালাচ্ছে। যদিও বিএনপি ছাত্রদের জনসমর্থনের প্রস্তাব দিয়েছিল এবং তার কিছু অনুসারী রাজপথে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, তবে দলটি সরাসরি মিছিল আয়োজনে জড়িত ছিল না। নিহতদের মধ্যে যদি কেউ থাকে, তাহলে তারা বিএনপি, জামায়াত বা অন্যান্য বিরোধী দলের লোক বলে মনে করা হচ্ছে ।
কোটা পদ্ধতি কীভাবে আন্দোলনের সূত্রপাত করেছে?
স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭২ সালে সরকারি চাকরিতে সংরক্ষিত কোটা চালু করা হয়েছিল। প্রথমে সরকারি চাকরির ৮০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা, একাত্তরে ক্ষতিগ্রস্ত নারী এবং দেশের দরিদ্র এলাকার মানুষদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। কোটার সামগ্রিক শতাংশ বছরের পর বছর ধরে বেড়েছে। প্রতিবন্ধী এবং সংখ্যালঘু মানুষদের জন্য বিশেষ বিভাগ যোগ করা হয়েছে; ২০১২ সাল থেকে কোটা ৫৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যার মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের বংশধরদের জন্য ৩০ শতাংশ, নারীদের জন্য ১০ শতাংশ, ‘অনগ্রসর জেলা’ (অর্থাৎ দেশের দরিদ্র অঞ্চল) এর বাসিন্দাদের জন্য ১০ শতাংশ, জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্য ৫ শতাংশ এবং ১ শতাংশ শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য। এটা প্রথম নয় যে ছাত্ররা কোটা পদ্ধতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে, যেটিকে বাংলাদেশে অনেকেই অন্যায্য বলে মনে করেন। ২০১৮ সালে অনুরূপ- যদিও ছোট-বিক্ষোভের পরে, আওয়ামী লীগ সরকার কিছু গ্রেডের সরকারি চাকরির জন্য কোটা বাতিল করে, আপাতদৃষ্টিতে সেই বছরের নির্বাচনের দৌড়ে এগিয়ে থাকার প্রয়াসে। মুক্তিযোদ্ধাদের বেশকিছু বংশধর পরবর্তীতে সরকারের সিদ্ধান্তকে অসাংবিধানিক দাবি করে আদালতে আপিল করেন। জুনের শুরুতে মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে হাইকোর্ট কোটা ব্যবস্থা পুনর্বহাল রাখে। সেই রায় প্রতিবাদের আগুনে ঘি দেয়ার মতো কাজ করে।
অনেক সরকারি সমালোচকদের জন্য, এই রায়টি সরকারের ইচ্ছার পাশাপাশি বিচারব্যবস্থার ওপর তার প্রভাব প্রতিফলিত করে। কোটার প্রতি প্রধানমন্ত্রী হাসিনার সমর্থন তার একটি বক্তব্যে প্রতিফলিত হয়। সম্প্রতি তিনি বলেন- ‘দেশের উচিত মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করা’। তার পিতা ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, যিনি আওয়ামী লীগের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং ১৯৭৫ সালে তাকে হত্যার আগ পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন; লীগ এখনো নিজেকে জাতীয় মুক্তির দল হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে। লেফটেন্যান্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান, একজন সামরিক শাসক যিনি শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার পর ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন, ১৯৭৮ সালে একটি কেন্দ্রবাদী শক্তি হিসেবে বিএনপি গঠন করেছিলেন। যদিও পরে এটি স্বাধীনতার বিরোধিতাকারী ইসলামপন্থিদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েছিলেন। হাসিনা এবং আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং যারা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্নতা প্রতিরোধ করেছিল তাদের মধ্যে যোগসূত্রকে ঘৃণার চোখে দেখে। মুক্তিযোদ্ধা কোটা সংরক্ষণ, যা হাসিনার পিতার দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল, এই বিভাজনগুলোকে শক্তিশালী করার একটি উপায়। মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের বংশধররাও আওয়ামী লীগের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী অংশ হিসেবে রয়ে গেছেন, কোটাকে রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান এবং মিত্র বাড়ানোর একটি মাধ্যম করে তুলেছে।
বিক্ষোভ যখন গতি পেতে শুরু করে, তখন সরকার সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগকে হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে বলে, সেইমতো ৭ই আগস্ট শুনানির দিন নির্ধারণ করা হয়েছিল। বিক্ষোভ চরম আকার ধারণ করে এবং দেশটি কার্যত লকডাউনের অধীনে চলে যায়। যা দেখে সুপ্রিম কোর্ট শুনানি এগিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয়। ২১শে জুলাইয়ে রায়ে শীর্ষ আদালত ব্যাপকভাবে কোটা ৫৬ থেকে ৭ শতাংশে নামিয়ে এনেছে, যার মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মীয়দের জন্য ৫ শতাংশ এবং জাতিগত সংখ্যালঘু, প্রতিবন্ধী এবং নন-বাইনারি লিঙ্গের লোকদের জন্য ২ শতাংশ রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণভাবে এগুলো সমস্ত গ্রেডের চাকরিতে প্রযোজ্য। অন্যদিকে, নারীদের জন্য কোটা বাতিল করা ছিল একটি আশ্চর্যজনক পদক্ষেপ, কারণ ছাত্ররা নারী ও অন্যান্য গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের জন্য এটি বজায় রাখতে চেয়েছিল।
প্রতিবাদ আন্দোলনের পেছনে অন্য কারণ আছে কি?
কোটা বিরোধী বিক্ষোভ বাংলাদেশে গভীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে শক্তি অর্জন করেছে। দেশের অর্থনীতি বহু বছর ধরে বর্ধনশীল ছিল- বিশেষ করে ১৯৯০ সালে সামরিক শাসনের অবসানের পর থেকে মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষকে দারিদ্র্য থেকে বের করে এনেছে। কিন্তু কোভিড-১৯ মহামারির পর থেকে সরকার মুদ্রাস্ফীতি, বিশেষ করে উচ্চ খাদ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সংগ্রাম করছে। তবে অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি এবং স্বজনপ্রীতি তার প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করেছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বেশ কয়েকটি হাই-প্রোফাইল দুর্নীতি কেলেঙ্কারি প্রকাশ পেয়েছে, যা অনেক বাংলাদেশির জন্য গভীর অর্থনৈতিক যন্ত্রণার সময়ে ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। ১৪ই জুলাই এক সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনা স্বীকার করেন যে তার একজন গৃহকর্মী কয়েক মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ সম্পদ অর্জন করেছেন। তিনি কীভাবে এত ধনী হয়েছিলেন তা তিনি বুঝতে পারেননি বলে দাবি করেন। কিন্তু অনেক বাংলাদেশির কাছে এটা অবাক হওয়ার কিছু নেই যে ক্ষমতার এত কাছে থাকা একজন ব্যক্তি এত সম্পদ অর্জন করতে পারে।
সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রেও দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে, যার মধ্যে অর্থ কোটা হলো সবচেয়ে বাস্তব উপাদান। অনেক বাংলাদেশি সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থাকে পচনধরা একটি সিস্টেম বলে মনে করে। শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারেন যে অনেক কথিত যোগ্যতাভিত্তিক পদ তাদের কাছে যায় যাদের ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে। একই সময়ে গ্রাজুয়েটরাও বৃহত্তর জনসংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি মাত্রার বেকারত্বের সম্মুখীন হয়, সরকারি চাকরিতে তারা তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে। ইতিমধ্যে জনমত জরিপ থেকে বোঝা যায় যে, আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে কর্তৃত্ববাদী প্রবণতা কোটা পদ্ধতিকে ক্রমশ অজনপ্রিয় করে তুলেছে। ২০১৩ সাল থেকে, কর্তৃপক্ষ কয়েক হাজার বিরোধী সদস্যকে বিভিন্ন অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করেছে। সক্রিয় গুম এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড একটি ক্রমবর্ধমান ঘটনা হয়ে উঠেছে। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশের র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আমেরিকা, এই অভিজাত বাহিনীর অনেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করা হয়। দেশের কঠোর সেন্সরশিপ আইন সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এক হাজারেরও বেশি লোককে গ্রেপ্তার করেছে, প্রধানত সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের জন্য।
অধিকন্তু, হাসিনা ২০০৮ সালের নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশে সত্যিকারের প্রতিযোগিতামূলক জাতীয় নির্বাচন হয়নি। ক্ষমতাসীন দল ভোটকে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দেখানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা সত্ত্বেও ৭৫ শতাংশ আসন জিতে নেয়- উদাহরণস্বরূপ, প্রায় ২০ শতাংশ আসন তারা হেরেছে ‘স্বতন্ত্র প্রার্থীদের’ কাছে যারা বাস্তবে ক্ষমতাসীন দলেরই সদস্য। কিন্তু ভোটদানের হার আনুষ্ঠানিকভাবে ৪২ শতাংশ দেখায় যার কারণে বাংলাদেশিরা বোকা বনেনি। প্রধান বিরোধী দল বিএনপি এর আগে ভোটকে সামনে রেখে সুষ্ঠু নির্বাচনী পরিবেশের দাবি মেনে নিতে সরকারকে চাপ দিতে গণআন্দোলন শুরু করেছিল। পুলিশ এবং ছাত্রলীগ ২০২৩ সালের অক্টোবরে একটি বড় সমাবেশ ভেঙে দেয় এবং অনেক বিএনপি নেতাকে জেলে পাঠানো হয়, দলটিকে ভোট বর্জন করতে প্ররোচিত করে।
কোটা বিরোধী বিক্ষোভ তাই রাজনৈতিক দৃশ্যপটকেও রূপান্তরিত করেছে, জনগণের অসন্তোষকে এমনভাবে কাজে লাগিয়েছে যেটা বিএনপি করতে পারেনি, পাশাপাশি একটি তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্বকে সামনে এনেছে রাজনীতিতে যাকে অচল বলে মনে করা হয়েছিল। এমনকি এতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যারা ধনী পরিবার থেকে এসেছে এবং কোটা পদ্ধতির অধীনে চাকরি পাওয়ার চেয়ে বিদেশে পাড়ি জমাতে বেশি আগ্রহী। প্রতিবাদী আন্দোলনে অনেক তরুণীর সম্পৃক্ততাও নজরে এসেছে।
ঢাকার এখন কী করা উচিত?
সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা পুনরুদ্ধার করতে এবং রাজপথে শান্তি ফিরিয়ে আনতে, আওয়ামী লীগ সরকারকে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে দেশকে প্রান্তিক অবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ নেয়া উচিত। সামরিক আইন প্রত্যাহার করা উচিত, ইন্টারনেট অ্যাক্সেস পুনরুদ্ধার করা উচিত এবং বিক্ষোভের সময় হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পুনরায় খোলার ব্যবস্থা করতে হবে এবং গত সপ্তাহে গ্রেপ্তার হওয়া ছাত্রদের মুক্ত করতে হবে। বাংলাদেশ সরকারকে অবিলম্বে নাগরিক অধিকারের প্রতি সম্মান পুনরুদ্ধার করতে এবং কোটা বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারীদের সঙ্গে আলোচনার জন্য অনুরোধ জানাতে বিদেশি অংশীদারদের এগিয়ে আসা উচিত। হাসিনা সরকারের কট্টর সমর্থক ভারতের উচিত বহুদলীয় গণতন্ত্র, সুশাসন এবং নাগরিক অধিকারের প্রতি সম্মান পুনরুদ্ধার করে বাংলাদেশকে স্থিতিশীলতার পথে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করা। আওয়ামী লীগের প্রতি নয়াদিল্লির সমর্থন দীর্ঘদিনের। কিন্তু বাংলাদেশে ভারতবিরোধী মনোভাবের মধ্যে এই কৌশল ঝুঁঁকিপূর্ণ হতে পারে- বিষয়টি একদিকে যেমন বাংলাদেশের প্রতিবেশীর জন্য খারাপ তেমনি বাংলাদেশের জনগণের জন্য উপকারী নাও হতে পারে। কোটা বিরোধী বিক্ষোভের উত্থান বাংলাদেশে একদলীয় শাসন কতোটা ভঙ্গুর তা চিত্রিত করেছে। সংলাপ এবং রাজনৈতিক সংস্কারের গুরুতর প্রচেষ্টার পরিবর্তে বিক্ষোভ দমন করার জন্য কর্তৃত্ববাদী পদ্ধতি কখনই দেশে স্থায়ী শান্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে না।
সূত্র: মানবজমিন।
তারিখ: জুলাই ২৭, ২০২৪
রেটিং করুনঃ ,