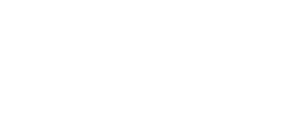লেখা:আজিজ হাসান।
সাম্প্রদায়িক হিংসার সূচনা ব্রিটিশ শাসনামলে
সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অর্মত্য সেনের স্মৃতিকথামূলক বই হোম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড: আ মেমোয়ার। বইটির ‘বাংলা ও বাংলাদেশের ধারণা’ শীর্ষক অধ্যায়ে উঠে এসেছে বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ঘিরে নানা স্মৃতি। অমর্ত্য সেন বাংলা ও বাঙালির ক্রমবিকাশের নানা পর্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। অবিভক্ত বাংলায় হিন্দু–মুসলমানের সম্পর্কের ধরন কেমন ছিল, সম্প্রীতির সেই সম্পর্ক একসময় বিষময় হয়ে উঠল। সেখান থেকে সরে এসে আবার ঐক্যবদ্ধ বাঙালি ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে একটি স্বাধীন দেশের জন্ম দিল। এই সংহতি কীভাবে এল, শক্তির জায়গা কোথায়—সে সবই অনুসন্ধান করেছেন অমর্ত্য সেন। তাঁর স্মৃতিকথার ‘বাংলা ও বাংলাদেশের ধারণা’ শীর্ষক অধ্যায়টির তিন পর্বের দ্বিতীয় অংশ আজ প্রকাশিত হলো। ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন আজিজ হাসান।
ঢাকা, কলকাতা ও শান্তিনিকেতনে আমাদের অনেক মুসলমান বন্ধু ছিল। ক্লাসের বিধিনিষেধের মধ্যেই স্বাভাবিকভাবে আমাদের দারুণ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। অধিকাংশ মুসলমান বন্ধুই আমাদের মতো সামাজিক অবস্থান থেকে এসেছিল। তবে তারা ছিল সংখ্যালঘু, ধনী পরিবারের হিন্দু শিক্ষার্থীদের তুলনায় তাদের সংখ্যা ছিল অনেক কম। নিজের দেখা ও পরিবারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, বিশ্ববিদ্যালয় পাস করা অভিজাত শ্রেণি, সরকারি কর্মকর্তা ও ডাক্তার, আইনজীবীর মতো পেশাজীবী এবং সম্পদশালী মধ্যবিত্তের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা।
এদিক দিয়ে উত্তর ভারতের তুলনায় এখানকার পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। উত্তর ভারতে অভিজাত শ্রেণির মধ্যে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব ছিল বেশ। উত্তরাঞ্চলীয় শহর লক্ষ্ণৌয়ে গেলে আমার কাছে সব সময় এই বৈপরীত্য ধরা পড়ত। মমতা মাসি (আমার কাছে লাবু মাসি) থাকায় আমি প্রায়ই সেখানে যেতাম। আমার মেসো শৈলেন দাশগুপ্ত ছিলেন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক। স্কুলশিক্ষার্থী থাকাকালে ওই ক্যাম্পাসে ঘুরতে আমার খুব ভালো লাগত। তবে লক্ষ্ণৌ পছন্দ করার পেছনে আমার কাছে বড় কারণ ছিল, সেখানে খালাতো ভাই সোমশঙ্কর (বাচ্চুদা) এবং খালাতো বোন ইলিনা ও সুমনার সঙ্গে সময় কাটানো।
লক্ষ্ণৌর সমৃদ্ধ সংস্কৃতির প্রতিও আমি মুগ্ধ ছিলাম। উচ্চবিত্তের মুসলমানরাই ছিলেন এই সংস্কৃতির ধারক। লক্ষ্ণৌর উচ্চবিত্ত শ্রেণি ঐতিহ্যগতভাবে ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের। তাদের মধ্যে শুধু একসময়ের শাসকেরাই নন, নবাবেরাও ছিলেন মুসলমান। লক্ষ্ণৌর অভিজাত মুসলমানদের আয়েশি ও শান্তধারার জীবনযাপনের চিত্র সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত চলচ্চিত্র শতরঞ্জ কে খিলাড়ি (১৯৭৭)–তে বেশ ভালোভাবে উঠে এসেছে।
মুসলিম শাসন
ঢাকায়ও মুসলমান নবাবেরা ছিলেন, তবে তাঁদের ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীর বাইরে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিপুলসংখ্যক বাঙালি মুসলমান খুব সম্পদশালী ছিলেন না। কয়েক শতাব্দী ধরে মুসলমান রাজারা বাংলা শাসন করলেও এটা ছিল বৈপরীত্য। ওই বাঙালি শাসকেরা হিন্দু উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে তাঁদের স্বস্তিদায়ক অবস্থান থেকে সরাতে চেয়েছিলেন বা তাঁদের ইসলাম গ্রহণে জোর করেছিলেন বলে মনে হয় না।
বহু ধর্মকে গ্রহণ করার বিষয়টি মোগলদের একটি সাধারণ নীতি ছিল। তা শুরু হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সম্রাট আকবরের আমল থেকেই। (যখন ধর্ম অবমাননার জন্য রোমের ক্যাম্পো দে ফিওরিতে জিওরদানো ব্রুনোকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়, তখন আগ্রায় ধর্মীয় সহনশীলতার গুরুত্বের ওপর বক্তৃতা দিচ্ছিলেন আকবর)। অনেক হিন্দু ইতিহাসবিদ পরবর্তী মোগল শাসনের, বিশেষ করে এক শতাব্দী পরে সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে, ‘সাম্প্রদায়িক’ চরিত্র নিয়ে সমালোচনামুখর হলেও আমার নানা ক্ষীতি মোহন সেন ওই ইতিহাসের জ্ঞান নিয়ে আপত্তি করতেন।
সাম্প্রদায়িক বিরোধের ওই বছরগুলোতে যখন আমি বেড়ে উঠছিলাম, তখন তিনি একে ‘কল্পিত ইতিহাস’ বলতেন। আওরঙ্গজেবের আদালত ও ঘনিষ্ঠ সহচরদের মধ্যে একটি বড় সংখ্যায় হিন্দু ছিলেন। ক্ষীতি মোহন বিষয়টি সামনে নিয়ে আসতেন। আমার মনে হয়, এ কারণেই তিনি ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক বিভাজন বৃদ্ধি এবং অসেন্তাষ ও সহিংসতা উসকে দেওয়ার পেছনে গোষ্ঠীগত মুসলিমবিদ্বেষী ইতিহাসের বড় ভূমিকা দেখতেন।
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে দূরত্ব বাড়ে ব্রিটিশ শাসনামলে। প্রথমে শুরু হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ঘোষণা দেন। এর আওতায় জমিদারদের স্থায়ীভাবে সরকারকে রাজস্ব দেওয়ার প্রথা চালু হয়। তাতে ইচ্ছেমতো খাজনা বাড়ানোর সুযোগ পেয়ে যান তাঁরা।
এই জমিদারদের অনেকেই ছিলেন হিন্দু। তাঁরা একটি শ্রেণি গড়ে তুলেছিলেন, যাঁরা জমির আয় থেকেই জীবন যাপন করতেন। তবে তাঁরা থাকতেন বহু দূরে এবং নিজেরা চাষাবাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। জমিদারদের খাজনা দিয়ে চলা প্রজারা তীব্রভাবে শোষণ–বঞ্চনার শিকার হতেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান।
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে দেশের অর্থনীতি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার কারণ ছিল, এই ব্যবস্থায় কৃষির উন্নয়নে দেওয়া প্রায় সব প্রণোদনা বন্ধ হয়ে যায় এবং ভূমির মালিকানার ভিত্তিতে বৈষম্য গেড়ে বসে।
অবিচারের শিকার মুসলমানরা
কলকাতার কয়েক বছরে একটি বড় সংখ্যায় হিন্দু জমিদারদের সম্পর্কে আমি জানতে পারি। তাঁরা ছিলেন ছোট–বড় জমিদার। ওই জমি থেকে তাঁরা নিয়মিত অর্থ পেতেন। পুরোপুরি অবিচারে ভরা ব্যবস্থা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে গবেষণা করেছেন ইতিহাসবিদ রণজিত গুহ (পরে বন্ধু ও সহকর্মী)। তিনি স্বীকার করেছেন, শহরবাসী এই জমিদার শ্রেণির (জমিতে অনুপস্থিত) একজন সদস্য হিসেবে নিজেও এই ব্যবস্থার সুবিধাভোগী ছিলেন:
লেখক (রণজিত গুহ) তাঁর তরুণ বয়সে, বাংলায় তাঁর প্রজন্মের আরও অনেকের মতো বেড়ে উঠেছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ছায়ায়। পরিবারের মতো তাঁর জীবিকাও আসত দূরবর্তী তালুক থেকে, যেখানে তাঁরা কখনো যাননি। লর্ড কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবিধাভোগীদের বংশধরদের মধ্য থেকে একটি ঔপনিবেশিক প্রশাসনের ক্যাডার কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য যা যা প্রয়োজন, সেগুলোর ওপর ভিত্তি করেই ছিল তাঁর শিক্ষা। তাঁর সংস্কৃতির জগৎ ছিল জমি থেকে পাওয়া মাখনের ওপর ভর করে বেঁচে থাকা মধ্যবিত্ত শ্রেণির মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে। সেখানে এখানকার আদি সংস্কৃতি, যা সাধারণ কৃষকেরা ধারণ করতেন, তার কোনো সংযোগ ছিল না।
আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসবিদ তপন রায় চৌধুরীও জমিদার পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। বর্তমান বাংলাদেশের বরিশালের জমিদার পরিবারের এই সদস্য লিখেছেন:
‘জমিদার মানে দরিদ্র হালচাষী কৃষকদের কাছ থেকে রাজকীয় সম্মান পাবেন।…যখন আমরা রায়তদের মুখোমুখি হতাম, তারা যেন আমাদের দেবতা জ্ঞান করে আচরণ করত।…বাঙালি জমিদাররা বিশ্বের এই অংশে এক শতাব্দীরও বেশি সময় পল্লী এবং কিছু মাত্রায় নগর সমাজেও প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে।’
এই রায়তদের কিছু ছিলেন নিচু শ্রেণির হিন্দু। অনেকে—বস্তুত তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান। এই অর্থনৈতিক অসমতার কারণে বাঙালি মুসলমানদের বিদ্বেষের রাজনীতিতে টানা ছিল খুবই সহজ। চল্লিশের দশকের মাঝামাঝিতে বাংলায় মুসলিম লীগের সাময়িক সাফল্য, যা ভারত ভাগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তার একটি জোরালো সম্পর্ক ছিল এই ভূমির মালিকানার সঙ্গে।
বিজ্ঞাপন
বাংলাদেশের মহান রাষ্ট্রনায়ক
আমি যখন স্কুলে পড়তাম, সেই সময়ের তুলনায় বাংলায় অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়েছে। তবে যে বিষয়টি পরিস্থিতি পুরোপুরি বদলে দিয়েছে, তা হলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবিচারের অবসান। ১৯৪৭–৪৮–এ রাতারাতি কীভাবে ধনী জমিদারদের বিলাসী জীবনযাপন উধাও হয়ে গেল, তা তপন রায় চৌধুরী বর্ণনা করেছেন। এটা বলা সংগত হবে, এই রাতারাতি বদল এমন একটি বাংলাদেশ তৈরি করল, যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি জোরালো অঙ্গীকার ছিল, যেমনটি সম্ভবত ১৯৪০–এর দশকে ছিল না। অবশ্য গল্পের আরও অংশ বাকি রয়ে গেছে, বিশেষ করে বাংলাদেশের মহান রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি দারুণভাবে বিকশিত হলো।
একসময় ‘ভূমির প্রশ্ন’ ছিল মুসলমানদের অসন্তোষের প্রধান কারণ। এর জন্যই এ কে ফজলুল হকের ধর্মনিরপেক্ষতা আটকে গিয়েছিল। কিন্তু এই সময়ে এসে হঠাৎ বিষয়টি আলোচনার বাইরে চলে গেল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আরও সুসংহত বাঙালি আন্দোলনের জায়গা তৈরি হলো। ভারত ভাগ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছরের কম সময়ের মধ্যে ১৯৫২ সালের বাংলা ভাষা আন্দোলন ছিল তার সূচনা।
একটি ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজন ছিল গঠনমূলক রাজনীতির বিকাশ ঘটানো। ওই বছরগুলোতে অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেই তা করা হয়েছিল।
এর জন্য প্রয়োজন ছিল একটি দূরদর্শী ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, যা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে এসেছিল। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, বঙ্গবন্ধু শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে আসা বাঙালির সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিশেষ ইতিহাসকে ধরতে পেরেছিলেন। সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণগুলোও বুঝতে পেরেছিলেন তিনি।
যখন আমি বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাসের কথা ভাবতাম, তা ঢাকা, কলকাতা বা শান্তিনিকেতন—যেখানকারই হোক না কেন, তখন এই বিষয়গুলো প্রাসঙ্গিকভাবে চলে আসত। বিশেষ করে আমরা কি ‘বাঙালি জনগণের’ কথা ঠিকভাবে বলতে পারছি, সেই প্রশ্নের জবাবে বিষয়গুলো আরও স্পষ্ট হয়ে উঠত।
একজন বাঙালি পরিচয় সব সময়ই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তা আমার পেশা, রাজনীতি, জাতীয়তা, মানবিকতাসহ আমার অন্যান্য সম্পৃক্ততার সবকিছু বিবেচনায় নিয়েই। আজকের যে বাঙালি পরিচয়, তার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণ রয়েছে।
১৯৩০–এর দশকের প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর হিবার্ট বক্তব্যে অক্সফোর্ডে শ্রোতাদের উদ্দেশে বলেছিলেন, তিনি এসেছেন তিনটি সংস্কৃতির মিলন থেকে—হিন্দু, মুসলিম ও ব্রিটিশ। এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠীতে নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি; বরং এর মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র গণ্ডিবদ্ধ হওয়ার চেয়ে বৃহত্তর পরিসরের পরিচিতির সগর্ব উদ্যাপনের প্রকাশ ঘটেছে।
রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ধর্মনিরপেক্ষতার স্বীকৃতি একজন বাংলাদেশি মুসলমানের ধর্মীয় পরিচয় কেড়ে নেয় না। এটা এই দাবির সঙ্গে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ যে মানুষের ধর্মীয় পরিচয় তাদের রাজনৈতিক পরিচয় থেকে ভিন্ন হতে পারে। একই কথা বলা যায় বাঙালি হিন্দুর ক্ষেত্রেও, তা তিনি বাংলাদেশ বা ভারত—যেখানেই থাকুন না কেন।
সূত্রঃ প্রথম আলো।
তারিখঃ সেপ্টম্বর ২৩, ২০২১
রেটিং করুনঃ ,