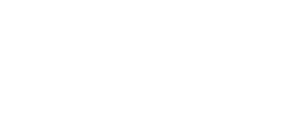১২ই মার্চ সমরেশ বসুর চির-বিদায়ের দিন।
সমরেশ বসুর জীবন নদী বয়ে চলেছিল জোয়ার ভাঁটায়। পড়েছে বাঁকের মুখেও। কিন্তু থেমে যাননি। লেখক সমরেশ ও পিতা সমরেশকে পাশপাশি রেখে স্মৃতিচারণ করলেন পুত্র — নবকুমার বসু
তাঁর লেখনী থেমে গেল যাত্রা অসম্পূর্ণ রেখেই। কিছু করার নেই। স্বয়ং বিধাতার সৃষ্টিও তো অসম্পূর্ণ। তবুও কালের বিচারে কিছু স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় তাঁর সৃষ্টি-বৈচিত্র নিয়ে। নিরন্তর আলোচনায় ভেসে থাকেন সৃষ্টিকর্তাটিও। এমনকী রয়েছেন মৃত্যুর তিরিশ বছর পরেও !!
সাল ১৯৮৭, সমরেশ বসুর দীর্ঘ প্রতীক্ষিত রামকিঙ্কর বেজ-এর জীবনভিত্তিক সুদীর্ঘ উপন্যাস ‘দেখি নাই ফিরে’ দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। মাস ছয়েকের মধ্যে উপন্যাস বেশ খানিকটা অগ্রসর হয়েছে। বাবা থাকতে এলেন যাদবপুরে আমাদের কাছে। তখন ওঁর শরীর ভাল যাচ্ছে না। দু’বার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। এ দিকে বিগত আট-দশ বছর ধরে বাবা প্রায় চিরুনি তল্লাশির মতো তন্নতন্ন করে রামকিঙ্করের জীবন, মেধা-মনন ও সময় সম্পর্কে তথ্য আহরণ প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছেন। আর ঠিক সেই সময়ই শরীর বাধা হয়ে দাঁড়াল। আমরা তখন প্রান্তবাসী। আমি ও আমার স্ত্রী রাখি দু’জনেই চিকিৎসক। যাদবপুরে আমার শ্বশুরালয় সংলগ্ন জমিতে একটি ছোট নার্সিংহোম তৈরি করেছি। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ নিজেরাই করি। ওই নার্সিংহোমে বিদেশ থেকে নেবুলাইজার পাম্প সহ আরও বেশ কিছু উন্নত যন্ত্রপাতি এনেছিলাম। সেই সময় বাবার চিকিৎসা করতেন কলকাতার নামী চিকিৎসকরা। বাবার শ্বাসকষ্টের জন্য ওগুলো ব্যবহার করা হত খ্যাতনামা ডাক্তারদের পরামর্শে। মানুষটা বেশ স্বস্তি পেতেন তাতে, আর আমরাও।
‘দেখি নাই ফিরে’-র শেষ কয়েকটি কিস্তি বাবা লিখেছিলেন আমাদের নার্সিংহোমে বসে। খামে করে পাণ্ডুলিপি আমিই গিয়ে ‘দেশ’ –এর তৎকালীন সম্পাদক সাগরময় ঘোষের হাতে দিয়ে আসতাম। লেখকের শারীরিক অবস্থার জন্য সম্পাদকের মুখে উদ্বেগের ছায়া আমি পড়তে পারতাম। বাবার তখন সান্ধ্য আড্ডা, কিঞ্চিৎ মদ্যপান সবই প্রায় বন্ধ। শুধু ডাক্তারদের বারণের জন্য নয়, ও সবে তাঁর ইচ্ছে নেই বুঝতে পারতাম। আমরা চেষ্টা করতাম যতটা বাবাকে যত্নে রাখা যায়, নিয়মে রাখা যায়। কারণ তিনি আমার বাবা হলেও তিনি বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত সাহিত্যিক সমরেশ বসু, তিনি কালকূট— বহু জনের কাছের মানুষ। তাঁর সুচিকিৎসা করা আমার বড় দায়িত্ব।
রামকিঙ্কর বেজ ছাড়া বাবার মাথায় তখন আর কিছু ছিল না। কোথায় যেন একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে ফেলেছিলেন। জীবনধর্মী উপন্যাস লেখার একেবারে পরিকল্পনাপর্বে সত্যজিৎ রায় পরামর্শ দিয়েছিলেন বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে লেখার জন্য। বাবা ভেবেছিলেন, কিন্তু স্থিতধী হয়েছিলেন নিজের ভাবনা ও উপলব্ধির উপর। মানুষ এবং শিল্পী হিসেবে রামকিঙ্কর অনেক বলিষ্ঠ চরিত্র বলে বাবা মনে করেছিলেন। রামকিঙ্করের প্রসঙ্গে বাবার বলা কিছু কথা আজও আমার মনে পড়ে। তিনি বলতেন, ‘‘রামকিঙ্কর যেন এক বিশাল ঠাকুরের মূর্তি আমার ঘাড়ে… বিসর্জন দিতে পারব, না কি দিতে গিয়ে আমিই তলিয়ে যাব…ভাবি মাঝে-মাঝে।’’ আরও একটি কথা বলতে শুরু করেছিলেন, ‘‘শান্তিনিকেতন এবং তখনকার নানান লোকজন সম্পর্কে যে সব তথ্য পেয়েছি … কাহিনি ঘটনা হিসাবেও সে সব সাগরদা দেশে ছাপতে পারবেন কি না কে জানে?’’ তৃতীয় পর্ব ‘রৌদ্রদগ্ধ দীর্ঘ বেলা’য় শুরু হচ্ছে রামকিঙ্করের পূর্ণ যৌবন কালের কথা। এই বারেই তো সেই সব কথা আসবে। আজ ভাবি, ঈশ্বরের কী বিচিত্র বিচার! এই তৃতীয় পর্ব সূচনার গোড়াতেই বাবার কলম থেমে গেল। অসমাপ্ত থেকে গেল বাংলা সাহিত্যের একটি কালজয়ী নির্মাণ। জানতে পেরেছিলাম ‘দেখি নাই ফিরে’ উপন্যাসের পাঁচটি পর্বের নামকরণ করেছিলেন এই রকম, ‘আরক্ত ভোর’, ‘সকালের ডাক— বিশ্বঅঙ্গনে’, ‘রৌদ্রদগ্ধ দীর্ঘ বেলা’, ‘ছায়া দীর্ঘতর’ এবং ‘অন্ধকারের আলো’। রামকিঙ্করের জীবনের গতি ও চলন অনুযায়ী ওই নামকরণ ও পর্বভাগ।
সমরেশ বসুর জীবনের শেষ দিকের কিছু দিন আমার জীবনের পরম প্রাপ্তি। কোনও এক অজানা কারণে এই তৃতীয় সন্তানটিকে কৃতজ্ঞ করতেই বুঝি খ্যাতনামা মানুষটি আমাদের কাছে থাকতে এসেছিলেন। বাবা হিসেবে তাঁর সঙ্গে আমার কোনও দিনই আদিখ্যেতা মেশানো মাখোমাখো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। বাবা-মা’র চরম দারিদ্র্য আর কষ্টের জীবনের চারটি খুদে সহযাত্রী ছিলাম আমরা চার ভাইবোন। কেমন ছিল সেই সব দিন!
উত্তর ২৪ পরগনার শ্যামনগর এবং জগদ্দলের মধ্যবর্তী গঞ্জ এলাকা, আতপুর। একটি আধা বস্তির দেড় কামরা টালির চালের নীচে আমাদের ছ’টি প্রাণীর বসবাস। ঘরের চেয়ে বাইরে-বাইরে ঘুরে বেড়ানোতেই আমরা স্বচ্ছন্দ বোধ করতাম। কেননা টালির ঘরের ফাটা মেঝের উপর জলচৌকি রেখে দোয়াতে ডোবানো কলম দিয়ে বাবা লিখতেন। ঘরের উলটো দিকে একফালি খোলা বারান্দায় তোলা উনুনে (ভাঙা বালতির উপর মাটি লেপে বানানো) মা গৌরী বসু, রান্না করতেন। মাঝে মাঝে দু’-চার পাতা লেখা কাগজ নিয়ে বাবা উঠে যেতেন মা’র কাছে। উবু হয়ে বসে, লেখা পড়ে শোনাতেন মাকে। মা মতামত দিতেন লেখা শুনে।
কেন জানি না, এই দৃশ্যটি আমার চোখে যেন মহৎ ছবি হয়ে আছে। মা আমাদের মাঝেমধ্যেই স্মরণ করিয়ে দিতেন, ‘‘তোদের বাবা একজন লেখক।’’ কিন্তু লেখক কী বস্তু! আমার সেই ছোট বয়সে কোনও ধারণা ছিল না এই ‘লেখক’ শব্দটি সম্পর্কে। অথচ বাবার সেই পরিচয় দিতে গিয়ে মায়ের চোখেমুখে একটা গৌরবের আলো যাতায়াত করত। এখন কেন যেন মনে হয়, আমার অবচেতন মনে সেই গৌরবের আলোর প্রতিফলন ঘটেছিল। পরবর্তী কালে, হয়তো সেই আলোতেই আমি ব্যক্তি ও লেখক সমরেশ বসুকে একটু একটু করে আবিষ্কার করেছিলাম, আবিষ্কার করেছিলাম আমার বাবাকে।
আতপুর থেকে নৈহাটিতে চলে এলাম আমরা। জীবনের পরিবর্তন এল। মনে আছে, আমরা নৈহাটিতে চলে আসার কিছু দিন পরেই ‘পথের পাঁচালি’ সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছিল নৈহাটি সিনেমা হলে। বাবা তখন মোটামুটি পরিচিত মানুষ। বাবার লেখা ‘গঙ্গা’ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে। ‘অমৃতকুম্ভের সন্ধানে’ ছবি করার জন্য সেই সময়ের বম্বের চিত্রপরিচালক বিমল রায় চিত্রস্বত্ব কিনেছেন। আমাদের জীবন যাপনে তখনও এমন কিছু পরিবর্তন ঘটেনি। এখনও মনে পড়ে, মা যেন সেই সময় থেকেই একেবারে দশভুজা হয়ে (নামেও তো গৌরী) সংসারটির হাল ধরেছিলেন। যার পিছনে একটাই উদ্দেশ্য, ‘ও মানুষটাকে শুধু লেখা ছাড়া আর কোনও ব্যাপারে না-টানা।’ রাজনৈতিক বন্দি হিসাবে জেল থেকে ফিরে এসে যখন ‘ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরি’র চাকরিটি খোয়ালেন, তখন চারটি শিশুসন্তান থাকা সত্ত্বেও মা বাবাকে বলেছিলেন, ‘‘যা হওয়ার হবে, কিন্তু তুমি আর চাকরি করতে যেও না।’’ ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়! চাল নেই, চুলো নেই, চাকরি নেই, ছ’জনের সংসার, তার মধ্যে চারটি কচি ক্ষুধার্ত মুখ সব সময়ে হাঁ-করে রয়েছে। এরই মাঝখানে একজন স্ত্রী তার স্বামীকে বলছেন, ‘‘তুমি লেখো! চাকরি করতে হবে না!’’ পাগলামি না কি আত্মবিশ্বাস! ভালবাসা না কি মরণঝাঁপ! জায়া-জননী-বন্ধু-কমরেড, কে এমন ভাবে পাশে দাঁড়ায়!
সমরেশ বসু কিন্তু আর ফিরে দেখেননি। ফিরে দেখার সময় তাঁর ছিল না। ছিল শুধু কয়েকজন সহৃদয় বন্ধু। কেউ পুরনো জামাকাপড় এনে দিতেন ছেলেমেয়ের জন্য। কেউ কলাটা-মুলোটা দিয়ে যেতেন। গ্রাম্য গোয়ালা মাকে বলেছিলেন, ‘‘পয়সা দিতে পারবে না বলে বাচ্চাদের দুধ বন্ধ করে দেব! অত অভাব আমার এখনও হয়নি! দুধ দেওয়া আমি বন্ধ করব না। যে দিন পয়সা হবে, সে দিনই দিও।’’ মা গান শেখাতেন। জামাকাপড় সেলাই করতেন। দেশভাগের পর মুসলমান পরিবারের পরিত্যক্ত টালির চালের দু’কামরা ঘরের একটিতে সংসার। দ্বিতীয় কামরাটি মা পুরো ছেড়ে দিয়েছিলেন বাবাকে। ‘মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মানুষটা সারা দিন লেখে’ সেই জন্য। সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে মা তখন রীতিমতো পরিচিত মফস্সল অঞ্চলে।
আমার মনে আছে, নৈহাটির বাড়িতে যে-ঘরে বসে বাবা লিখতেন, তার মেঝে ফুঁড়ে টালির চালের গোল ফাঁক দিয়ে উঠে গিয়েছে এক সুদীর্ঘ নারকেলগাছ। ও ভাবেই তৈরি সেই বাড়ি। অতীতে ওই অঞ্চলের নাম ছিল নারকেলবাগান। ঘর ঘেঁষা ঝোপ-জঙ্গল আর এঁদো পোড়ো জমি মিলিয়ে ছিল কাঠা তিনেক। ওই টালির ঘরের মধ্যেই দেখেছি, বাবার উপন্যাস ‘গঙ্গা’ নিয়ে নির্মিত ছবির ইউনিট চলে এসেছে। ত্রিবেণীতে আউটডোর করতে এসে ওঁরা চলে এসেছিলেন আমাদের বাড়ি। স্ক্রিপ্ট পড়া হল। রাজেন তরফদার, দীনেন গুপ্ত, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, রুমা গুহঠাকুরতা, নিরঞ্জন রায়, সলিল চৌধুরী, সীতা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সংলাপ বলছেন আর বাবা নিজে তাঁদের উচ্চারণ ঠিক করে দিচ্ছেন। সলিল চৌধুরী হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইতে লাগলেন, মা-এসে গলা মিলিয়েছিলেন। হঠাৎ আকাশে কালো মেঘ। মুহূর্তে পরিচালক রাজেন তরফদারের নির্দেশে সকলে ছুটলেন ন্যাচারাল পরিবেশে, আলো-মেঘ-বৃষ্টিতে শ্যুট করতে। বাবাও ছুটলেন ধুতিতে মালকোঁচা মেরে। এখনও যেন কানে শুনতে পাই, বাবা মাকে চেঁচিয়ে বলছেন, ‘‘বুড়ি, (মায়ের ডাকনাম) আমিও যাচ্ছি। কখন ফিরব জানি না, চিন্তা কোরো না।’’ আমরা তখন নেহাতই ছোট, কিন্তু বিপুল উৎসাহে সব দেখছি, আত্মস্থ করে ফেলছি।
সমরেশ বসুর জীবননদী বয়ে চলেছিল জোয়ার-ভাঁটায়। পড়েছে বাঁকের মুখেও। কিন্তু থেমে যায়নি। উত্তরোত্তর গতিও সঞ্চারিত হয়েছিল। না, তৎকালীন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি আর প্রতিভাবান এই লেখকের পাশে দাঁড়ায়নি। তাঁর কলমের উষ্ণতা পার্টি ব্যবহার করতে চেয়েছিল রাজনৈতিক প্রয়োজনে। কিন্তু তাঁর সংসারটি কী ভাবে টিকে থাকবে, তার কোনও হদিশ দেয়নি দল। দিশাহারার মতো লেখক পৌঁছে গিয়েছিলেন, আনন্দবাজার পত্রিকার কানাইলাল সরকার, সাগরময় ঘোষের কাছে। সূচনা হয়েছিল জীবনভর সম্পর্কের বাঁধনের। কমিউনিস্ট পার্টি পরবর্তী কালে আজীবন বিদ্রুপ করেছে এবং নেতিবাচক সমালোচনা করেছে সমরেশ বসুর। এমনকী মৃত্যুর পরেও তৎকালীন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ‘লেখকের দ্বিতীয় মৃত্যু’ বলে করে পার্টির কাগজে দীর্ঘ নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। অথচ ছোটবেলা থেকেই দেখেছি, নৈহাটিতে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা বাড়িতে আসতেন নিয়মিত এবং বাবা-মা দু’জনেই যথেষ্ট চাঁদা দিতেন তাঁদের!
মানুষটার ব্যক্তিজীবনেও পরিবর্তন হতে শুরু করেছিল। বদল তো স্বাভাবিক। পরিবর্তন যে প্রকৃতিরই নিয়ম। সমরেশ বসু ব্যক্তি এবং লেখক, উভয় দিক দিয়েই যে ব্যতিক্রমী সন্দেহ নেই। তা ছাড়াও কোথায় যেন এক বিপরীতধর্মিতার জটিল রসায়ন, যাকে হয়তো প্যারাডক্সিক্যাল ইমোশন বলা যায়, ক্রিয়াশীল হয়ে উঠতে শুরু করেছিল মানুষটার মধ্যে। সাহিত্যে যাঁর কোনও ফাঁকি নেই, জীবনে তাঁর অদৃশ্য ফাঁক রচিত হয়ে যাওয়াই কি নিয়তি! না, রচিত তো হয়ে যায় না, রচনা করা হয় বলেই রচিত হয়। এই রচনাই কি মনস্তত্ত্বের জটিল রসায়ন? আপাতদৃষ্টিতে যে আচরণ বা সম্পর্কের কোনও ব্যাখ্যা মেলে না, মনে হয় চূড়ান্ত বৈপরীত্যে ভরা, অথচ সে দিকেই তীব্র গোপন আনুগত্যের আশ্লিষ্ট হয়ে যাওয়া…কী জানি, বারবার নানা ভাবে, তলিয়ে ভাবার চেষ্টা করেও মনে হয়েছে, সমরেশ বসুর জীবনকাহিনিতে সে যেন এক বিস্মিত বিভ্রান্ত অধ্যায়। জীবনশিকারি লেখক তিনি, নিজেকে সে ভাবেই চিনিয়ে দিয়েছেন, বলেছেন, ‘‘সাহিত্যের থেকে জীবন বড়।’’ সেই মানুষই কবুল করেছেন, ‘‘কাঠ খেয়েছি, আংরা বেরুবে।’’ কোথাও অনুতাপ ছিল কি? বা কিঞ্চিৎ আত্ম-তিরস্কার?
হ্যাঁ, তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন ও বাস্তববাদী, আত্মবিশ্বাসী লেখকটির আরও একটি সম্পর্কে ভেসে যাওয়ার অপরিণামদর্শিতার অধ্যায় সেটি। সম্পর্ক-রচনার পাত্রীটির সঙ্গে তাঁর তো রুচি-সংস্কৃতি-বুদ্ধিমত্তা কোনও কিছুরই মিল ছিল না। অথচ নিশির ডাকের মতো টানে ষাটের দশকে নিত্য ছুটে যেতেন পূর্ব কাঁঠালপাড়ার সেই বাড়িতে। যেখানে থমথম করত এক মধ্যযুগীয় পরিবেশ। বড় দালানকোঠা, ছাদে কড়িবরগা, জানালায় খড়খড়ি, ছাদ থেকে জলনিকাশির বাঘমুখ নালা, বড় ইঁদারা, ফাটা চাতাল… আমাদের মামার বাড়ির সেই নিঝুম পরিবেশে খ্যাতিমান লেখকটি ছুটে যেতেন, একমাত্র একটি যুবতীর আকর্ষণে! যে আকর্ষণে ধারাবাহিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তাঁর পুত্র-কন্যারা। অসম্মানে, গ্লানিতে বিধ্বস্ত-ছারখার-ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর সেই ‘বুড়ি’!
একটা গোলমাল বিভ্রান্তি লেগেই থাকে। অথচ দিন যায় তার পরেও। লেখকের খ্যাতি-সুনাম-স্বাচ্ছন্দ্য… কোনও কিছুই পড়ে থাকে না, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। মানুষটা যেন পাঁকাল মাছের মতো। কাদা-পাঁকের মধ্য দিয়ে চললেও, তাঁর গায়ে আলোর ঝলকানি। ছেলে-মেয়ে স্ত্রীকে ফেলে পাতলেন কলকাতায় নতুন সংসার, দ্বিতীয়া স্ত্রী। স্বচ্ছলতা। অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে আর একটি সন্তানলাভ!
অন্য সংসারটির দায়ভার তখন দিনে দিনে কমে আসছে। না, কমেও যেন কমছিল না। জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্বশুরালয়ে, তা সত্ত্বেও কোথায় যেন টানাপড়েন ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র জীবিকা সন্ধানে নেমেও পিতৃনির্ভরশীল এবং বিবাহিত। এই অধম ডাক্তারির ছাত্র এবং হস্টেলবাসী, কনিষ্ঠা কন্যাও পাঠরতা। আর সর্ব অর্থে সমরেশ বসুর অর্ধাঙ্গিনী, কমরেড ও জীবনসঙ্গিনী গৌরী বসু তখন নৈহাটির বাড়ি আর বেঁচে থাকার অবলম্বন হিসেবে গড়ে তোলা শিক্ষায়তন ‘ফাল্গুনী’ নিয়ে হাঁটছেন ক্লান্ত পদক্ষেপে। শরীরে ভাঙন, তবুও চলেছেন।
বাবা কিন্তু তখনও নিয়ম করে প্রতি সপ্তাহে নৈহাটি যেতেন। তাঁর উপস্থিতিতে প্রাণময় হয়ে উঠত বাড়ির পরিবেশ। সান্ধ্য আড্ডা বসত দোতলায় বাবার ঘরে। কোনও সময় শামিল হয়েছি সেই আড্ডায়। নৈহাটি-ভাটপাড়া-হালিশহর-কাঁচড়াপাড়ার সমরেশ-ভক্তরা এসে জুটতেন আমাদের বাড়িতে। কোনও সময় বাবা-মা দু’জনে বসে কথা বলতেন। গৌরী বসু তার মধ্যেও খেয়াল করতেন, লেখকের চোখেমুখে পরিশ্রমের ছাপ। মানুষটার বয়সও তো বসে নেই! আমাকে বলতেন, ‘‘খুব ধকল যাচ্ছে লোকটার!’’ আর কী আশ্চর্য, তার মধ্যেই ঝলসে ওঠার মতো গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনি, গোয়েন্দা কাহিনি, কিশোর কাহিনি লিখছেন। ‘দেশ’-এ ধারাবাহিক ‘কোথায় পাব তারে’ ‘যুগ যুগ জিয়ে’ লিখেছেন। ‘বিবর’ পর্যায়ের পরে নক্ষত্রের মতো রচনা ‘বাথান’, ‘টানাপোড়েন’, ‘তিন পুরুষ’, ‘শিকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে’, ‘মহাকালের রথের ঘোড়়া’। কালকূট ঝুঁকেছেন মানস ভ্রমণের দিকে: ‘পৃথা’, ‘জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য’, ‘শাম্ব’…
না, মানুষটাকে ঠিক মেলাতে পারি না। মনে হয়, বৈপরীত্যের মধ্যেই জীবনের আকাশ ছুঁতে চান এক ব্যতিক্রমী শিল্পী।
আমি সেই হস্টেল জীবন থেকেই বিচ্ছিন্ন, প্রান্তবাসী। এক শহরে থেকেও পাড়ের কিনারা ধরে হাঁটি। ১৯৮০-তে মাতৃবিয়োগের পর থেকেই মনে হতো, বাবা মানুষটা সব কিছুর মধ্যে, সব কিছু নিয়েও বড় নিঃসঙ্গ। একটু-একটু করে আবার যোগাযোগ হতে লাগল বাবার সঙ্গে। আমার স্ত্রী ও আমি তখন পায়ের তলায় মাটির সন্ধান করছি। প্রতিদিনের রোজগার থেকে বাঁচিয়ে ঘর উঠছে একটু-একটু করে। বাবার সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়। জিজ্ঞেস করি, ‘‘সন্ধেবেলা কী করছ? চলে এসো না এখানে!’’
পিতা-পুত্রের মধ্যে কথা হতো ঘরবাড়ি-সংসার-অতীত-দায়দায়িত্ব-একাকীত্ব আর রামকিঙ্কর নিয়ে। মনে হত, মানুষটা যেন একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচতেন আমাদের কাছে এসে।
বোধহয় একঘেয়েমি এসে যাচ্ছিল কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের তথাকথিত ইন্টেলেকচুয়াল আড্ডায়, ক্লাবে। খ্যাতিমান মানুষদের দায় বেশি, নিঃসঙ্গতা তাঁদের অনিবার্য। মনে হত, যেন লেখার জন্যই নিজেকে আরও গুটিয়ে নিচ্ছিলেন বাইরে থেকে। বারবার বলতেন, ধারাবাহিক উপন্যাস মানে তো মেল ট্রেন, চলতে শুরু করলে থামানো যাবে না।
ব্যতিক্রমী মানুষ ও লেখক সমরেশ বসু প্রয়াত হলেন ১২ মার্চ, ১৯৮৮ সালে। তাঁর লেখনী থেমে গেল যাত্রা অসম্পূর্ণ রেখেই। কিছু করার নেই। স্বয়ং বিধাতার সৃষ্টিও তো অসম্পূর্ণ। তবুও কালের বিচারে কিছু স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় তাঁর সৃষ্টি-বৈচিত্র নিয়ে। নিরন্তর আলোচনায় ভেসে থাকেন সৃষ্টিকর্তাটিও। এমনকী রয়েছেন মৃত্যুর তিরিশ বছর পরেও!
কৃতজ্ঞতা – সোমনাথ সেনগুপ্ত ও দেবনাথ সেনগুপ্ত ( সূত্র : আনন্দবাজার পত্রিকা )
সূত্র: সংগৃহিত।
তারিখ: মার্চ ১৩, ২০২১
রেটিং করুনঃ ,