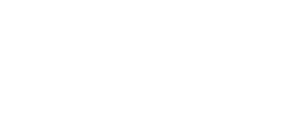‘‘দেবের আনন্দ ধাম দেবানন্দপুর গ্রাম/ তাহে অধিকারী রাম রামচন্দ্র মুনসী।/ ভারতে নরেন্দ্র রায় দেশে যার যশ গায়/ হয়ে মোর কৃপাদায় পড়াইল পারসী।।’’— হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামকে নিয়ে এই পঙ্ক্তি লিখেছিলেন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। স্বভাবতই, সে গ্রাম জড়িয়ে ছিল মহাকবির নামের সঙ্গেই। তবে তার পরে বাংলা সাহিত্যের মহাকাশে আর এক নক্ষত্র জন্ম নিলেন এই দেবানন্দপুরেই। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১২৮৩ সালের ৩১ ভাদ্র এক গরিব ব্রাহ্মণ পরিবারে কথাসাহিত্যিকের জন্ম।
ছেলের সাড়াশব্দ না পেয়ে আদরের সুরে মা ডাকলেন— ‘‘ন্যাড়া, ও ন্যাড়া, খাবি আয় বাবা!’’ তবু উত্তর নেই। রান্নাঘরে ন্যাড়াকে পাওয়া গেল না। গোয়ালঘরেও না। রেগে গিয়ে স্বামীকে বললেন, ‘‘হ্যাঁগা, নিজে তো বেশ খেয়েদেয়ে এখন ঐ ছাইপাঁশ নভেলগুলো পড়ছো! আর ওদিকে ছেলেটা না খেয়ে পাড়ায় টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেদিকে কি খেয়াল আছে?’’ বাবা অবশ্য হাসিমুখে বললেন, ‘‘যাবে আর কোথায় ভুবন! দেখ, ও হয়তো ঐ রায়েদের আমবাগানে ফড়িং ধরছে।’’ সত্যিই তাই। আমবাগানে সুন্দর একটা ফড়িং ধরতে গিয়ে পাখা ভেঙে ফেলেছে ‘বাউন্ডুলে’ ছেলে। তাই তার মন খারাপ। অবশেষে বাবার কথায় ফড়িংটাকে বাগানে রেখেই বাড়ির পথে ফেরে ন্যাড়া। আর প্রতিজ্ঞা করে, ‘‘আমি একটাও ফড়িং বাক্সে রাখবো না। সব উড়িয়ে দেবো।’’ বাবা অবাক হন— ‘‘সামান্য একটা ফড়িংয়ের জন্যে কি কাঁদতে আছে রে?’’
তবে, বালক ন্যাড়া ওরফে শরৎচন্দ্রের লেখাপড়ার প্রতি প্রায় কোনও আগ্রহ ছিল না। গ্রামের পিয়ারী পণ্ডিতের পাঠশালায় ছেলেকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন বাবা মতিলাল। ছেলের সেখানে না যাওয়ার কারণটা যে ঠিক কী, সেটা বুঝতে পারতেন না তিনি। এক দিনের কথোপকথন এ রকম:
—ন্যাড়া, পাঠশালায় যাস না কেন?
—ভাল লাগে না যে।
—না পড়লে বড় হবি কি করে?
—পড়লে বুঝি বড় হওয়া যায়?
—হ্যাঁ রে, হ্যাঁ।
তার পরে শরৎ পাঠশালায় গেল। তাতে গোল বাড়ল। দুষ্টুমিতে অতিষ্ঠ করে তুলল পিয়ারী পণ্ডিতকে। এক দিন পাঠশালায় নতুন ছেলে ভর্তি হয়েছে। শরৎ তার কাছে জানতে চাইল, সে লিখতে পারে কি না। জবাবে ‘না’ শুনে ‘তবে দে, তোর লেখা লিখে দিই’ বলে স্লেটে বড় বড় অক্ষরে লিখল ‘তুই একটা গাধা’। তার পর হঠাৎ হেঁচে তন্দ্রাচ্ছন্ন পণ্ডিতকে জাগিয়ে তুলল। তাঁর চোখ পড়ল নতুন ছেলেটির উপরে, ‘‘কী ছাঁদের আঁক কচ্ছিস দেখি।’’ স্লেট হাতে নিয়েই চিল-চিৎকার, ‘‘বলি, হ্যাঁ রে ছুঁচোমুখো—‘‘তুই একটা গাধা’’ তার মানে কি রে উল্লুক? কেন লিখেছিস জবাব দে।’’ ছেলেটি কাঁপতে কাঁপতে শরতের দিকে তাকায়। আমবাগানে পলায়ন বিনা তার আর কোনও উপায় রইল না।
সন্ধেয় বাড়ি ফিরে বই নিয়ে বসত না শরৎ। ভাল লাগত না। ঠাকুমার কাছে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প শুনতে পছন্দ করত। আর এক এক সময়ে আশ্চর্য হয়ে বাবার লেখার ঘরে গিয়ে বসত। মোটা খাতায় মতিলালের সুন্দর হস্তাক্ষর দেখে জানতে চাইত, সেগুলো কী। মতিলাল বলতেন, ‘‘আগে বড় হ’ তারপর ওসব বুঝবি।’’ অবশেষে সে বাবার কাছ থেকে উত্তর আদায় করেই ছাড়ে। ওগুলো নাটক। আসলে মতিলালের পরিবারের আর্থিক অবস্থা একেবারেই ভাল ছিল না। তার মধ্যেই যাত্রাপালা লেখার কাজ চলত। কাজেই পাড়া-প্রতিবেশীর ব্যঙ্গ জুটত।
পিয়ারী পণ্ডিতের পাঠশালা থেকে ছাড়িয়ে শরৎকে ভর্তি করা হল সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্যের নতুন বাংলা-স্কুলে। কিন্তু অর্থকষ্ট বাড়তে থাকায় অবশেষে হুগলির পাট চুকিয়ে ১৮৮৬ সালে সপরিবার ভাগলপুরে শ্বশুরবাড়ি চলে গেলেন মতিলাল। সেখানে সবাই জানে, শরৎ খুব ভাল ছেলে। ছাত্রবৃত্তি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভর্তিও করে দেওয়া হল তাকে। কিন্তু এত দিন সে এতই কম শিখেছে যে অকূলপাথারে পড়ল। শরতের একটা গুণ— জেদ ছিল ষোলো আনা। সহপাঠীদের চেয়ে পিছিয়ে থাকার ‘অগৌরব’ সহ্য হল না। লেখাপড়ায় ভাল হয়ে উঠল দুরন্ত বালক। মামাবাড়িতে দারুণ গল্পের আসর বসত। তাতেও আগ্রহভরে যোগ দিল সে। এক দিন শরতের মাসিমা কুসুমকামিনী দেবী ‘কপালকুণ্ডলা’ পড়ছেন। হঠাৎ শরতের প্রশ্ন, ‘নবকুমারকে কাপালিক কেটে ফেলবে?’ তার পরে নিজেই বলে, ‘কেটে ফেললেই তো গল্প শেষ হয়ে যাবে। ও কাটবে না।’
দেবানন্দপুরের সঙ্গ ছাড়ার পর অনেকটাই বদলে যায় শরৎ। সেটা বুঝতে পেরে খুশি হয়ে মা ভুবনমোহিনীও স্বামীকে বলেন, “শোরো আজকাল কী শান্ত হয়েছে!” ১৮৮৭ সালে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাশ করে স্থানীয় ইংরেজি স্কুলের সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হয় সে। প্রথম বছর বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান তো পায়ই, পেয়ে যায় একেবারে ডাব্ল প্রোমোশন! খেলাধুলো আর দুষ্টুমির বদলে মন আকৃষ্ট হয় স্বাস্থ্যচর্চার দিকে। যেমন ভাবা, তেমনই কাজ। কয়েক জন সঙ্গীকে নিয়ে তৈরি করে ফেলে স্বাস্থ্যচর্চার দল।
বেশ কিছু দিন শ্বশুরবাড়িতে কাটানোর পরে আত্মীয়দের মধ্যে গোলযোগ বাধতে শুরু করায় সপরিবারে পৈতৃক ভিটেতে ফিরতে হয় মতিলালকে। ১৮৮৯ সালে শরৎ ফেরে দেবানন্দপুরে। লেখাপড়া চলতে থাকে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে। পুরনো বন্ধুবান্ধব ফের জুটে যেতেই থিয়েটারের নেশা চেপে বসে। গ্রামের জমিদার নবগোপাল দত্ত মুন্সীর পুত্র অতুলচন্দ্র খুব ভালবাসতেন শরৎকে। তাকে মাঝে মাঝে কলকাতায় এনে থিয়েটার দেখিয়ে বলতেন, অভিনয়ের বিষয়বস্তু গল্পের মতো করে লিখতে পারলে পুরস্কার দেবে। শরৎ লিখত এবং পুরস্কারও আদায় করত।
শরতের কাব্যপ্রীতির সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে সাংসারিক অনটন। ১৮৯৪-এ ফের ভাগলপুরেই ফিরতে হয় মতিলালদের। শরতের সাহিত্যপ্রেম নিয়ে ‘বাল্যস্মৃতি’তে পাওয়া যায় দু’টি ঘটনা। লিখছেন, “এই সময় বাবার দেরাজ থেকে বের করলাম ‘হরিদাসের গুপ্তকথা’ আর বেরুলো ‘ভবানী পাঠক’। গুরুজনদের দোষ দিতে পারিনে। স্কুলের পাঠ্য তো নয়, ওগুলো বদ-ছেলের পাঠ্য পুস্তক। তাই পড়বার ঠাঁই নিতে হলো আমাকে বাড়ীর গোয়ালঘরে। সেখানে আমি পড়ি, তারা শোনে।” আর এক জায়গায়, “পিতার নিকট হইতে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকারসূত্রে আর কিছুই পাইনি।… কিন্তু এখনো মনে আছে ছোটবেলায় তাঁর অসমাপ্ত লেখাগুলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছিলাম। কেন তিনি এইগুলি শেষ করে যাননি— এই বলে কত দুঃখই না করেছি। অসমাপ্ত অংশগুলি কি হতে পারে ভাবতে-ভাবতে আমার অনেক বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে।”
এ বার তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজিয়েট স্কুল। আবার ভাগলপুরের পুরনো বন্ধুরা। শরৎ যে পরিবারে বড় হচ্ছিল, সেখানে উকিল হওয়াটাই জীবনের লক্ষ্য। অতএব প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এফএ পড়া শুরু হল। আলাপ হল রাজেন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গে। এই রাজুই হল ‘শ্রীকান্ত’র ইন্দ্রনাথ। নির্জন গড়ের ধারে বসে মনের আনন্দে বাঁশি বাজাত রাজু— আকৃষ্ট হয়েছিল শরৎ। ঘুড়ি ওড়ানো, তামাক খাওয়া, গান-বাজনা, রাজুর সঙ্গে হঠাৎ হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া, আবার ফিরে আসা, একসঙ্গে নৈশ-অভিযানে জেলেডিঙিতে মাছ-চুরি, যাত্রা-থিয়েটারের মহড়া— চলতে লাগল বন্ধুত্ব যাপন।
১৮৯৫ সালে প্রয়াত হলেন শরতের মা ভুবনমোহিনী। বিহ্বল মতিলাল শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বাসা বাঁধলেন খঞ্জরপুর গ্রামে। সেখানেই আবার সমবয়সিদের নিয়ে ‘সাহিত্য-চক্র’ গড়ে তুলল শরৎ। চলতে লাগল লেখালেখি। সেখানেই এক দিন পঠিত হল ‘অভিমান’ গল্পটি। বন্ধুমহলে লেখক হিসেবে পরিচিতি তৈরি হতে লাগল। সাহিত্যের ভূত এমন ভাবেই ঘাড়ে চেপে বসল যে, এফএ পরীক্ষায় ফল ভাল হল না। পরিবারের মুখের দিকে তাকিয়েও চিরদিনের মতো কলেজের পাট চুকিয়ে সাহিত্য জগতেই আশ্রয় নিল সে।
শুরু হল ‘কুঁড়ি সাহিত্যিক’ নামে এক সাহিত্য-সভা। বার হতে লাগল হাতে লেখা পত্রিকা ‘ছায়া’। তবে সাহিত্য করে সংসার চলে না। চললও না। জমিদার শিবশঙ্কর সাউকে ধরে তাঁর রাজবনেলী স্টেটে একটা চাকরি জোটানো গেল। তবে টেকানো গেল না। বাবার সঙ্গে মন কষাকষি হল। বাড়ি ছাড়ল ছেলে।
ঘুরতে ঘুরতে হাজির মুজফ্ফরপুরে। ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকার অন্যতম কর্ণধার প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের কলমে— “একদিন সন্ধ্যার সময় ক্লাবে তাঁদের দলবল মিলিত হলেন— এমন সময় গেরুয়া-বসনধারী এক তরুণ সন্ন্যাসী এসে পরিষ্কার হিন্দী ভাষায় সবিনয়ে লিখবার সরঞ্জাম প্রার্থনা করলেন।” দেহাতি ছদ্মবেশ ধরা পড়ল। পরিচয় মিলল শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এ দিকে অনুরূপা দেবীর লেখা থেকে জানা যায়, এ সময়ে নিরুদ্দিষ্ট শরতের খাতা থেকে একের পর এক গল্প উদ্ধার হয়েছে— ‘বোঝা’, ‘অনুপমার প্রেম’, ‘বামুনঠাকুর’, ‘কোরেল গ্রাম’, ‘চন্দ্রনাথ’, ‘বড়দিদি’। মুজফ্ফরপুরে বসেই ‘ব্রহ্মদৈত্য’ নামে এক উপন্যাস লেখা শুরু করে শরৎ। এখানে আলাপ হয় মহাদেব সাউ নামে এক জমিদারের সঙ্গে। ‘শ্রীকান্ত’র কুমারসাহেব তিনিই। অবশেষে ১৯০৩-এ পিতৃবিয়োগের খবর শুনে খঞ্জরপুর ফেরে শরৎ।
তখন একটা কাজের বড়ই দরকার। কলকাতায় মামা উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে হাজির হয় শরৎ। উপেন্দ্রনাথের ভাই লালমোহনের কোর্টের কাগজপত্র ও দলিলের অনুবাদের কাজ মেলে। তবে কলম কি আর থামে? ভাগলপুরের যোগেশচন্দ্র মজুমদারের লেখা থেকে জানা যায়— “তিনি ১৩০৯ সালে একবার ‘কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতা’য় তাঁহার মাতুল সুরেন্দ্রনাথের নামে রচনা পাঠাইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন।” গল্পটির নাম ‘মন্দির’। আসলে শরৎ নিজ নামে কিছু প্রকাশ করিতে একান্ত অনিচ্ছুক ছিল।
এ দিকে মাত্র তিরিশ টাকা বেতনে কাজ করতে শরতের তখন আপত্তি। উপেন্দ্রনাথের কাছে কিছু টাকা ‘কর্জ’ চায় সে। বলে, “এখানে থাকতে আমার মন চাইছে না, উপীন। রেঙ্গুনে নাকি ভাগ্য ফেরে।” রেঙ্গুন তার ঠিক অচেনাও নয়। মাসিমা সেখানে থাকতেন। ১৯০৩ সালে ২৭ বছর বয়সে জাহাজে করে বর্মায় গিয়ে হাজির হন শরৎ। মাসিমারা খুবই বড়লোক। তাঁদের ঘরের ছেলে হয়ে থাকতে শুরু করেন তিনি। সুতরাং জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আসে। কিছু দিনের মধ্যে বর্মী ভাষাটাও শিখে নেন। অকস্মাৎ মাসিমার স্বামী উকিল অঘোরবাবু প্রয়াত হওয়ায় তাঁরা রেঙ্গুনের পাট চুকিয়ে চলে যান কলকাতা। ফের পথে বসেন শরৎ! তবে এই যাত্রায় কায়ক্লেশে চাকরি জুটিয়ে ফেলেন।
বস্তুত, বর্মাবাসের আগে পর্যন্ত খানিকটা দুর্ভাগ্যের কবলে পড়েই এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত কেবল অনিশ্চয়তার মধ্যে ছুটে বেড়াতে হত শরৎকে। রেঙ্গুন তাঁকে কিছুটা সুস্থিতি দেয়। প্রবাসকালে মনের বৈরাগ্যও কিছুটা ক্ষীণ হয়ে আসে। সংসারী হওয়ার সাধ জাগে। বিয়েও করেন।
‘‘একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ যখন সাহিত্য সেবার ডাক এলো, তখন যৌবনের দাবী শেষ ক’রে প্রৌঢ়ত্বের এলাকায় পা দিয়েছি। দেহ শ্রান্ত, উদ্যম সীমাবদ্ধ— শেখবার বয়স পার হয়ে গেছে। থাকি প্রবাসে, সব থেকে বিচ্ছিন্ন, সকলের কাছে অপরিচিত, কিন্তু আহ্বানে সাড়া দিলাম, ভয়ের কথা মনেই হোলোনা।’’
প্রায় ১৮ বছর পরে, ১৯১৩ সালে, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিজের পুনরাগমনকে এ ভাবেই দেখেছিলেন শরৎচন্দ্র। নবপ্রকাশিত ছোট পত্রিকা ‘যমুনা’তে এ সব লেখা ছাপা হতে শুরু করে।
গল্পের শুরুটা অবশ্য বেশ কয়েক বছর আগেই। ১৩১৪ বঙ্গাব্দ। সরলা দেবী তখন ‘ভারতী’র সম্পাদক এবং সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় কলকাতা থেকে তাঁর নামে কাগজ চালান। সৌরীন্দ্রমোহন জানতেন, রেঙ্গুন যাওয়ার আগে নিজের লেখাগুলি সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে রেখে গিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। সেখান থেকে ছোট উপন্যাস ‘বড়দিদি’ আনিয়ে তিন কিস্তিতে ‘ভারতী’তে ছাপিয়েও দেন। লেখকের অনুমতি নেননি, কারণ নেওয়ার চেষ্টা করলে মিলত না! লেখা নিয়ে হইচই পড়ে। শরৎচন্দ্রের অজ্ঞাতেই রসজ্ঞ পাঠক ও সমালোচক মহলে তাঁকে নিয়ে আগ্রহ তৈরি হয়। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃতি অনিবার্য। কাজেই কালের নিয়মে হারিয়ে যান শরৎচন্দ্র। এর পর কী ভাবে ফিরলেন, তাঁর বয়ানেই জানা যায়।
শুধু ফেরা নয়, অবিশ্বাস্য দ্রুততায় পাঠকমহলে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। কয়েক বছরের মধ্যে চাকরি ছেড়ে পাকাপাকি সাহিত্যিক। ‘চরিত্রহীন’ যখন বই আকারে বেরোল, দাম সাড়ে তিন টাকা। প্রথম দিনই বিক্রি হয়েছিল সাড়ে চারশো কপি। বাংলা সাহিত্যে এই রেকর্ড আর কারও ছিল না। পরে তা ভাঙে শরৎচন্দ্রের ‘পথের দাবী’র সৌজন্যে। রেঙ্গুনে অজ্ঞাতবাসের জন্য গেলেও সেখােনই আত্মপ্রকাশ করেন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ‘রামের সুমতি’, ‘পথনির্দ্দেশ’, ‘বিন্দুর ছেলে’, ‘নারীর মূল্য’, ‘চরিত্রহীন’-এর জন্ম সেখানেই।
‘যমুনা’ থেকে ‘ভারতবর্ষ’। এ বার কলম চালিয়ে অর্থলাভও হতে লাগল। তবে কেবল ‘ভারতবর্ষ’ নয়, শরৎচন্দ্র ছড়িয়ে পড়লেন ‘বঙ্গবাণী’, ‘নারায়ণ’, ‘বিচিত্রা’য়। কোনও কোনও উপন্যাস সরাসরি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল, যেমন ‘বামুনের মেয়ে’। এ পর্বে লিখলেন ‘বিরাজ-বৌ’, ‘পণ্ডিত-মশাই’, ‘বৈকুণ্ঠের উইল’, ‘মেজদিদি’, ‘দত্তা’, ‘পল্লীসমাজ’, ‘অরক্ষণীয়া’, ‘নিষ্কৃতি’, ‘গৃহদাহ’, ‘দেনা-পাওনা’, ‘নববিধান’, ‘মহেশ’, ‘পথের দাবী’, ‘শেষ প্রশ্ন’… স্বল্প কালপর্বে পরপর এতগুলি জনপ্রিয় ও অমর সৃষ্টি করে যেতে পারেন কেউ? সত্যিই বিস্ময়কর!
‘নারায়ণ’ পত্রিকার গল্পের জন্য শরৎচন্দ্রকে একটা সই করা চেক পাঠিয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ, সঙ্গে লিখেছিলেন, ‘আপনার মতন শিল্পীর অমূল্য লেখার মূল্য স্থির করবার স্পর্দ্ধা আমার নেই, টাকার ঘর শূন্য রেখে চেক পাঠালুম, এতে নিজের খুসি-মত অঙ্ক বসিয়ে নিতে পারেন!’ এবং নিজের অসাধারণতার মূল্যও নির্ধারণ করেছিলেন শরৎচন্দ্র— একশো টাকা! দেশবন্ধুর পদক্ষেপেই সাহিত্যিকের জনপ্রিয়তা অনুমেয়।
বাংলা রঙ্গালয়ে শরৎ-সাহিত্যের চাহিদা তৈরি হয়েছিল। সর্বাগ্রে অভিনীত হয়েছিল ‘বিরাজ-বৌ’। নাট্যরূপ দিয়েছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিনীত হয় স্টার থিয়েটারে। তার পর শিশিরকুমার ভাদুড়ী। ‘ভারতী’তে ‘দেনা-পাওনা’র নাট্যরূপ দিয়েছিলেন শিবরাম চক্রবর্তী, নাম ‘ষোড়শী’। অভিনয় করালেন শিশিরকুমার। সাফল্যের পরে অভিনীত হল ‘রমা’, ‘চরিত্রহীন’, ‘অচলা’, ‘বিজয়া’।
নাটকের পরে চলচ্চিত্র। এবং শিশিরকুমার। নির্মিত হল ‘আঁধারে আলো’র চিত্ররূপ। তার পরে ‘দেবদাস’, ‘শ্রীকান্ত’, ‘বিজয়া’, ‘পণ্ডিত মশাই’ ইত্যাদি। তাঁর লেখা দেশি-বিদেশি ভাষায় অনূদিত হতে থাকল। এক কথায়, সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের উত্তরণ ও উত্থান রূপকথার মতো। হেমেন্দ্রকুমার রায় বর্ণনা করেছিলেন, ‘যৌবনে যে-শরৎচন্দ্রের দেশে মাথা রাখবার ছোট্ট একটুখানি ঠাঁই জোটে নি, ট্যাঁকে দুটি টাকা সম্বল ক’রে যিনি মরিয়া হয়ে মগের মুল্লুকে গিয়ে পড়েছিলেন, প্রৌঢ় বয়সে তিনিই যে দেশে ফিরে এসে বালিগঞ্জে সুন্দর বাড়ী, রূপনারায়ণের তটে চমৎকার পল্লী-আবাস তৈরি করবেন, মোটরে চ’ড়ে কলকাতার পথে বেড়াতে বেরুবেন…’ সত্যিই, তাঁর দূর বা নিকটজনেরা ভাবতেও পারেননি।
রেঙ্গুন থেকে ফিরে শিবপুরে বাড়ি ভাড়া নিলেও ভিড় আর ভাল লাগছিল না শরৎচন্দ্রের। তাই পাণিত্রাসে (বা সামতাবেড়) নিরালায় বাড়ি বানান। বাগানঘেরা দোতলা বাড়ি, লেখার ঘরে বসে রূপনারায়ণ দেখা যায়। কখনও লিখতেন, পড়তেন, ভাবতেন। বাগানে গাছেদের সেবা করতেন, পুকুরে মাছেদের খেতে দিতেন।
তবে আদর্শ জীবনে জরা আসে, রোগব্যাধি বাসা বাঁধে। শরৎচন্দ্রের অসুখ ছিলই। এক সময়ে প্রত্যেক দিন জ্বর আর শরীরময় যন্ত্রণা হতে থাকল। চিকিৎসকের নিষেধ সত্ত্বেও জোর করে পাকস্থলীতে অস্ত্রোপচার করালেন। তারিখটা ১২ জানুয়ারি। চার দিন পরে ১৩৪৪-এর ২ মাঘ
৬১ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন শরৎচন্দ্র। বিরাট শোভাযাত্রায় কেওড়াতলা মহাশ্মশানে জনপ্রিয় সাহিত্যিকের শেষকৃত্য হয়েছিল।
বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী লেখেন, “আমাদের দেশের প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের সাধারণ নিয়মানুসারে বঙ্কিমের প্রতিভার শক্তি পঁয়তাল্লিশ বৎসরের পর মন্দীভূত হইয়া আসিল।” শরৎচন্দ্রকে দেখলে কি সে কথা বলতেন? তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ চল্লিশের কোঠায় গিয়ে প্রকাশিত হয়। তাঁর জীবনকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়— দেবানন্দপুর-ভাগলপুর, ব্রহ্মদেশ, হাওড়া-শিবপুর, সামতাবেড়-কলকাতা। সাহিত্যসাধনাও চার পর্বে। ভাগলপুরে ছোট সাহিত্যগোষ্ঠী। ব্রহ্মদেশে ‘বড়দিদি’ প্রকাশের পরে খ্যাতির সূচনা। দেশে প্রত্যাবর্তন। অবশেষে সাহিত্য সাধনার সূত্র ধরেই শিখরে আরোহণ।
এই গগনচুম্বী জনপ্রিয়তার ব্যাখ্যা করেন অজিতকুমার ঘোষ, “শরৎচন্দ্র সোজাভাবে, স্পষ্ট ভাষায় ও দুঃখ বেদনার কারুণ্যে সিক্ত করিয়া সমাজের সমস্যা তুলিয়া ধরিলেন এবং আমাদের প্রচলিত সংস্কার, নীতিবোধ ও ধর্মবোধের অন্যায় ও জবরদস্তি চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন। ইহার ফলে আমাদের বদ্ধ অচলায়তনের দ্বার যেন হঠাৎ খুলিয়া গেল, এবং সেই মুক্ত দ্বার দিয়া যত আলো ও বাতাস আসিয়া মুক্তির আনন্দে আমাদিগকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।”
বাংলা সাহিত্য কোনও গরিবকে ধনী করে তুলেছে, এমন বোধ হয় শরৎচন্দ্রের আগে সে ভাবে কল্পনা করা যেত না। দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী। রবীন্দ্রনাথ জমিদার। শরৎচন্দ্র এক এবং একমাত্র সাহিত্যেরই জোরে দু’পায়ে ভর দিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পেরেছিলেন।
ঋণ: দরদী শরৎচন্দ্র: মণীন্দ্র চক্রবর্তী, সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র: হেমেন্দ্রকুমার রায়, শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার: অজিতকুমার ঘোষ। ( ছবিগুলি -শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান দেবানন্দপুরের পৈত্রিক বাড়ি ও প্যারী পন্ডিতের পাঠশালা, বাজেশিবপুরের বাড়ি,যা বর্তমানে হেরিটেজ হিসেবে ঘোষিত। দেবানন্দপুর শরৎ স্মৃতি সংগ্রহশালা থেকে প্রাপ্ত। )
সূত্রঃ মলাট থেকে সংগৃহিত।
তারিখঃ সেপ্টম্বর ১৫, ২০২১
রেটিং করুনঃ ,