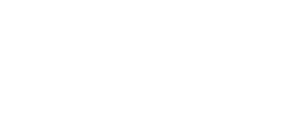শাসক যখন জনগণের হাতে শাসক বদলের ক্ষমতা রাখতে চান না, তখন শাসকেরা জনগণকেই বদলে দেন। তখন নির্বাচন অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু ভোট হয় না। সেই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি (জনগণ) হন অবাঞ্ছিত। তখন গণতন্ত্রের চালিকা শক্তি জনপ্রতিনিধিত্ব নিজেই অচল হয়ে যায়। ভোটাধিকার হারানো জনগোষ্ঠীকে তখন আর যা-ই বলা হোক, সংবিধানে বর্ণিত জনগণ বলা যায় না। এই জনগণের তাহলে কী করণীয়? গত সপ্তাহে ঠাকুরগাঁওয়ের এক নির্বাচনী সভায় কেন্দ্রীয় মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদা বেগম বলেন, ‘যাঁদের মনে ধানের শীষের সঙ্গে প্রেম আছে, তাঁরা কী করবেন? ১৩ তারিখে ঠাকুরগাঁও ছেড়ে চলে যাবেন। ১৩ তারিখ সন্ধ্যার পরে তাঁদের দেখতে চাই না। তাঁদের ভোটকেন্দ্রে আসার কোনো প্রয়োজন নাই।’ যাঁরা বিশেষ একটি দলকে সমর্থন করবেন না, তাঁদের দেশছাড়া করার হুমকিও প্রায়ই শোনা যায়।
পছন্দমতো ভোট দেওয়া কত বিপজ্জনক, তা–ও বুঝিয়ে দিয়েছেন লক্ষ্মীপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নুর উদ্দিন চৌধুরী ওরফে নয়ন। এই মহাত্মন প্রকাশ্যে ঘোষণা করে বলেছেন, ‘ইভিএম এমন এক সিস্টেম, নৌকার বাইরে কেউ ভোট দিলে ধরি হালান যায়…কত নম্বর ভোট নৌকার বাইরে গেছে, তা ধরি হালান যায়।’ তাঁরা বিচ্ছিন্ন কেউ নন, তাঁদের কথা বাস্তবতার বাইরে নয়।
কী হচ্ছে, তা নির্বাচন কমিশন এবং তাদের নিয়োগদাতা সরকারই ভালো জানে। কিন্তু বিগত ১০ বছরের কোনো নির্বাচনেই অধিকাংশ মানুষ ভোট দিতে পারেননি। মানুষ জানে, ভোট দেওয়া নিরাপদ নয়, স্বাধীন মতপ্রকাশ করা আত্মঘাতী। দেশের খবর এখন বিদেশি গণমাধ্যম থেকে জানতে হয়।
যদি ভোট না থাকে, ভিন্নমত অবৈধ বলে গণ্য হয়, তাহলে রাজনৈতিক দলের থেকে কাজ কী? নির্বাচনী গণতন্ত্রের প্রাণভোমরা হলো বহুদলীয় রাজনীতি। নির্বাচনই যদি না হবে, তাহলে রাজনৈতিক দলের আর কাজ কী? সরকারি দল না হয় উন্নয়নের টাকাকড়ি নিয়ে ব্যস্ত, বিরোধী দলের তো একটা প্রণোদনা থাকতে হবে যে ভালোভাবে কাজ করলে জনগণের ভোট পাওয়া যাবে। সেই সুযোগ বন্ধ করা মানে ঘোষণা না দিয়ে রাজনীতি নিষিদ্ধ করে দেওয়া। অতীতে এ কাজ সামরিক শাসকেরা করেছেন, এখন বেসামরিক লেবাসেই যথেষ্ট।
রাজনীতি যতই চেতনার কথা বলুক, এর গোড়ায় রয়েছে ক্ষমতা ও সম্পদের ভাগ পাওয়ার প্রতিযোগিতা। রাষ্ট্র করারোপ ও অন্যান্যভাবে যে আয় করে, তা কোন শ্রেণির লোক কতটা পাবে, কীভাবে তা বাঁটোয়ারা করা হবে, সেটাই রাজনীতির মূল মর্ম। তাই ভোট সংগ্রহের প্রতিযোগিতা মানে সম্পদ ও সুযোগ হাত করার প্রতিযোগিতা। রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুবিধার দরজা কাদের জন্য কতটা খোলা হবে, তা ঠিক করাও রাজনীতির আরেকটি প্রধান কাজ।
সুতরাং নির্বাচন যখন সরকারদলীয় এক নেতার ভাষায় ‘বিনা ভোট রীতি’তে হয়, তখন রাজনীতি অচল হয়, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো গোষ্ঠীর হাতের হাতিয়ার হয়। এ অবস্থায় প্রতিষ্ঠানগুলো ভেঙে পড়তে থাকে। তখন বিরোধী দলগুলোর মধ্য দিয়ে সমাজের যে যে অংশ সম্পদ ও সুযোগের ন্যায্য ভাগ পেতে চায়, তারাই শুধু দেউলিয়া হয় না, জনগণের বড় অংশও বঞ্চিত হয়। তখন সম্পদ কেবল একটা গোষ্ঠীর হাতে জমা হয়, ধনী ও গরিবের ব্যবধান অনেক বাড়ে, দারিদ্র্য ও ক্ষমতাহীনতা মানুষকে নাজুক অবস্থায় ফেলে দেয়। দুর্বল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাধারীরা তখন অর্থনীতিতে অবদান রাখতেও ব্যর্থ হয়। অক্ষমতা ও অভাব যখন সমার্থক, তখন কেবল অস্তিত্ব রক্ষার চেয়ে বেশি কিছু করার শক্তি থাকে না তাদের। একটি দেশ এভাবে ব্যর্থতার চোরাবালিতে ডুবতে থাকে।
২০১২ সালে হোয়াই ন্যাশনস ফেইল: দ্য অরিজিনস অব পাওয়ার, প্রসপারিটি অ্যান্ড পভার্টি (কেন দেশের পতন ঘটে: ক্ষমতা, সমৃদ্ধি এবং দারিদ্র্যের উৎস) বইটি প্রকাশ করেন ড্যারন এসিমগলু ও জেমস এ রবিনসন নামের দুই অর্থনীতিবিদ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ওপর ৩০০টির বেশি গবেষণাকর্ম বিশ্লেষণ করে তাঁরা জাতিসমূহের উন্নতির সূত্রগুলো মেলে ধরেন। তাঁরা দেখান, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের চরিত্রের মধ্যেই কোনো দেশের উত্থান বা পতনের কারণ নিহিত। তাঁরা দুই ধরনের প্রতিষ্ঠানের তুলনা করেছেন, একটা হলো নিষ্কাশনমূলক (এক্সট্রাকটিভ), সরল ভাষায় বললে শোষণমূলক। আরেকটা হলো ইনক্লুসিভ বা অন্তর্ভুক্তিমূলক। শোষণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলো সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে রাজনৈতিক নীতিনির্ধারণ ও আয় বণ্টনের প্রক্রিয়া থেকে বের করে দেয় (দমনের মাধ্যমে)। বিপরীতে সমাজের বৃহত্তর অংশকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় জড়িত করে তাদের হিস্যা বুঝিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে চলে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান। নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানগুলো মোটামুটি এ কাজ করে থাকে। যদি তারা সেটা করতে ব্যর্থ হয়, তখন জনগণ তাদের ভোটের মাধ্যমে সরিয়ে দেয়।
গণতন্ত্র, ভোটাধিকার, মতপ্রকাশ, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে সমন্বয়মূলক প্রতিষ্ঠানগুলো জীবন্ত থাকে। গণতান্ত্রিক পরিবেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলো জনগণের অধিকার পাহারা দেয়, যাতে ক্ষমতাসীন এলিটরা একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে না পারে। এককথায়, বহুদলীয় গণতন্ত্র না থাকলে টেকসই উন্নয়নও অসম্ভব হয়ে পড়ে।
কেউ কেউ চীনের একদলীয় শাসনে বিপুল উন্নতির কথা বলেন। কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়। চীনের শীর্ষ নেতৃত্বের স্তরে সমন্বয় কম থাকলেও অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রণোদনা কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান থেকেই এসেছে। ষাটের দশকের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের হানাহানি বন্ধ হয়েছিল রাজনৈতিক সিদ্ধান্তেই। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সেখানে দুর্নীতির পথের কাঁটা। চীনের অর্থনৈতিক বিকাশ আরও ঘটলে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকেও তাল মিলিয়ে উদার হতে হবে। তাই চীন আমাদের দোহাই হতে পারে না। তা ছাড়া চীনের অর্থনীতি উৎপাদনমুখী, আমাদের চলমান অর্থনীতি অনেকটাই আত্মসাৎমুখী। ঋণখেলাপ, ব্যাংক লুট, সম্পদ পাচার তার উদাহরণ। একচেটিয়া শাসন ছাড়া এ রকম একচেটিয়া দুর্নীতি চলতে পারত না। নির্বাচনব্যবস্থার ধ্বংস তাই রাজনৈতিক দুর্ঘটনা শুধু নয়, অর্থনৈতিক বঞ্চনারও কারণ। উচ্চাভিলাষী জনগণ তখন কেবল টিকে থাকাকেই সফলতা মনে করতে শুরু করে।
সূত্র: প্রথম আলো
লেখক: ফারুক ওয়াসিফ সাংবাদিক ও লেখক
তারিখঃ ফেব্রুয়ারী ১৮, ২০২১
রেটিং করুনঃ ,